02/10/2026 বাংলাদেশে মামদানির জনপ্রিয়তার কারণ, পরিচয়ের রাজনীতি নাকি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রতি সমর্থন
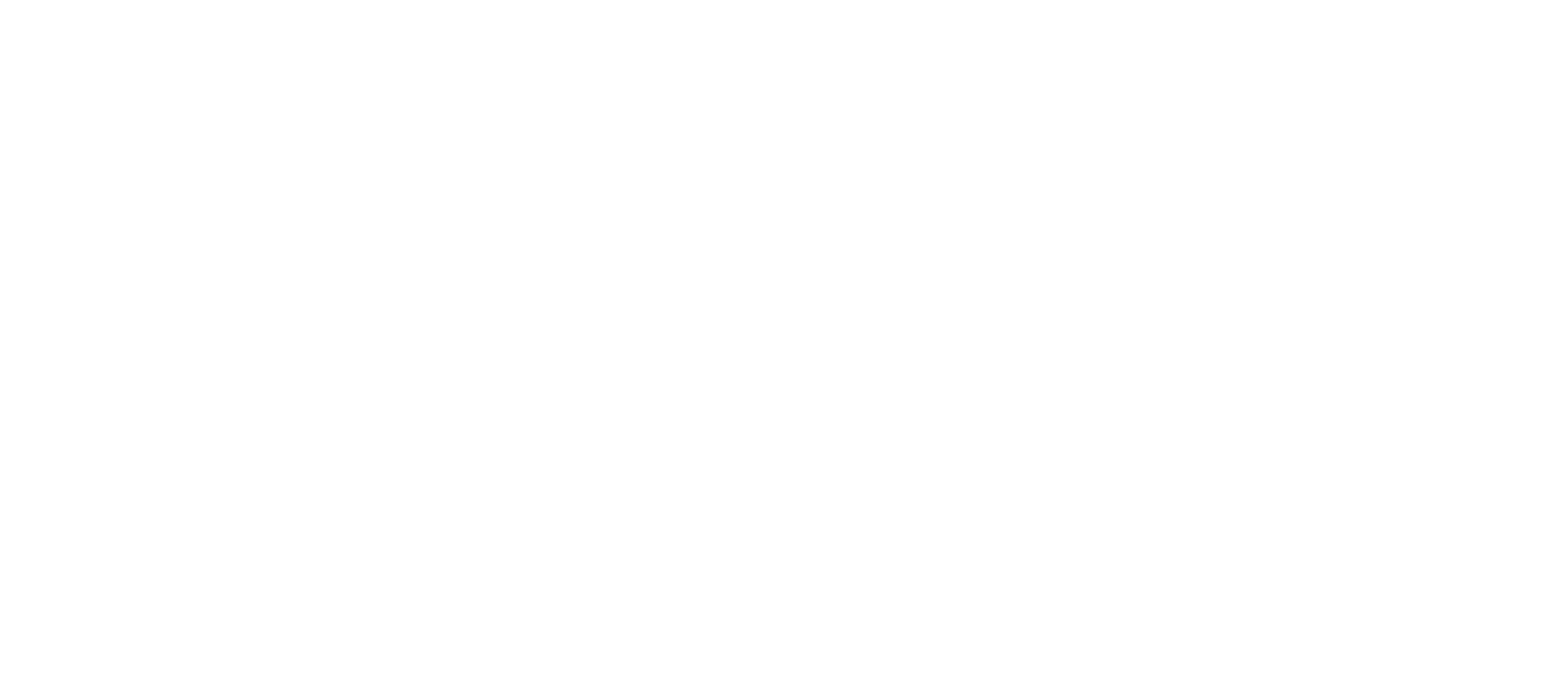
বাংলাদেশে মামদানির জনপ্রিয়তার কারণ, পরিচয়ের রাজনীতি নাকি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার প্রতি সমর্থন
মুনা নিউজ ডেস্ক
৫ নভেম্বর ২০২৫ ১৮:৩০

একজন জনপ্রতিনিধির কাছে ভোটারেরা কী চায়? স্বভাবতই মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা। বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানি (৩৪) এসব প্রত্যাশা পূরণের আশ্বাস দিয়ে স্থানীয় ভোটারদের আকৃষ্ট করেছেন। কিন্তু আটলান্টিকের ওপারের এক তরুণ বঙ্গোপসাগর পাড়ের বাংলাদেশিদের মন জিতলেন কী করে।
বুধবার সকালে মামদানির জয়ের খবর গণমাধ্যমে আসার পর থেকেই বাংলাদেশে বসবাসকারী অনেকে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এসব পোস্টের ক্যাপশনে একটি সাধারণ শব্দগুচ্ছ ছিল। সেটি হলো- ‘নিউ ইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র’।
প্রশ্ন হলো- কেবল মুসলিম বলেই কি মামদানি ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করেছেন? নাকি এর পেছনে আছে ‘আইডেন্টিটি পলিটিক্স’ (পরিচয়ের রাজনীতি) কিংবা ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো ব্যক্তির প্রতি মৌন সমর্থন?
আটলান্টিক-বঙ্গোপসাগর সংযোগ
জয় নিশ্চিতের পর মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন মামদানি। তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে বেজে ওঠে ২০০৪ সালে মুক্তি পাওয়া হিন্দি সিনেমা ‘ধুম’ এর টাইটেল ট্র্যাক ‘ধুম মাচালে’।
এমন ঘটনা মামদানির নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকেই ঘটছে। নিউ ইয়র্কের মতো অভিজাত শহরে তাঁকে কখনো কখনো রাস্তায় প্ল্যাকার্ড হাতেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। আন্তরিকতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ভারত, পাকিস্তানি কিংবা নিউ ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সঙ্গে।
উগান্ডায় জন্ম ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মামদানি নিজেকে পরিচয় দেন দক্ষিণ এশীয় মুসলিম বলে। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর প্রচারণা, গণপরিবহনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ছবি এবং বাংলা শব্দযুক্ত বক্তব্যও ছড়িয়ে পড়ে। এই বহুসাংস্কৃতিক পরিচয়ই গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক মাধ্যমের বদৌলতে সংযোগ তৈরি করে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশি মানুষের সঙ্গে। যা এই অঞ্চলের মানুষের প্রবাসজীবনের সংগ্রাম, পরিচয় সংকট ও আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্পের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে।
ফলে নিউ ইয়র্কের মতো বিশ্বনগরে দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত একজনের উত্থান অনেক বাংলাদেশির মাঝে ‘আমাদেরই কেউ’ মনোভাব তৈরি করে। প্রশ্ন হলো- এই প্রক্রিয়া ঘটে কীভাবে?
আইডেন্টিটি পলিটিক্স ও রেপ্রেজেন্টেশন থিওরি
মানুষ যখন নিজের জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কারও সঙ্গে সংযোগ অনুভব করে- সেটিকে বলে ‘আইডেন্টিটি পলিটিক্স’। অন্যদিকে ‘রেপ্রেজেন্টেশন থিওরি’ বলে, জনগণ তখনই কাউকে নিজের প্রতিনিধি ভাবে, যখন তাদের অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষা সেই নেতার কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়। নির্বাচনী প্রচারণায় মামদানি বাসা ভাড়া, পরিবহন, শিশুর যত্ন, নিম্ন-আয়ের মানুষের জীবনসংগ্রাম নিয়ে কথা বলেছেন। যেগুলো বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত বিষয়।
এ সংক্রান্ত একটি ব্যাখ্যা ১৯৭৯ সালেই দিয়ে রেখেছেন পোল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের সামাজিক মনোবিজ্ঞানী হেনরি তাজফেল ও জন সি টার্নার। সোশ্যাল আইডেন্টিটি থিওরিতে তারা বলেছেন, মানুষ নিজের মতো আরেক মানুষের প্রতি সহজাত সহানুভূতি তৈরি করে। মামদানির মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় পরিচয় সেই দলগত সংযোগকে জোরদার করেছে।
তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। অর্থ্যাৎ, ক্ষমতা চর্চার বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা মানুষেরা ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরেও কাল্পনিক ঐক্য গঠন করে। সে সূত্র ধরে বলা যায়, মামদানির সঙ্গে বাংলাদেশিদের ঐক্য গঠন হয়েছে, অভিবাসন, বর্ণ, সামাজিক মর্যাদা ও বসবাসের নিরাপত্তা বিবেচনায়।
দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসনবিরোধী কঠোর নীতিগ্রহণ করেছেন। শুল্ক আরোপ কিংবা ক্ষমতার চূড়ায় থেকে তাঁর আত্মকেন্দ্রিক প্রচার অন্য দেশের মানুষেরও বিরক্তির কারণ হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কিত খবরের মন্তব্যগুলোর দিকে নজর রাখলেই তা বোঝা যায়। মামদানি শুরু থেকেই এসব নীতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন। নিজেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। অভিবাসী হিসেবে তুলে ধরতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। শেতাঙ্গদের প্রতি ট্রাম্পের পক্ষপাতেরও সমালোচনা করেছেন।
অর্থ্যাৎ, ধর্মীয় কিংবা ভাষার পরিচয়ের বাইরেও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের নীতি ও ক্ষমতার কাঠামো বিরোধী মানসিকতা- মামদানির সঙ্গে ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংযোগ স্থাপন করেছে।
মামদানির ‘ট্রাম্প কার্ড’
নিউ ইয়র্কে বাড়িভাড়া ও জীবনযাত্রার ব্যয় বর্তমানে বড় রাজনৈতিক ইস্যু। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মামদানি তাঁর প্রচারণায় বলেছেন, নিউ ইয়র্ক শুধু ধনীদের নয়, শ্রমজীবী মানুষের শহর হতে হবে। তিনি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ, সাশ্রয়ী আবাসন ও বিনামূল্যে গণপরিবহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন- যা নিম্নআয়ের ভোটারদের আকৃষ্ট করেছে।
ভোটের আগের জনমত জরিপে ১৮-৩৪ বছর বয়সী ভোটারদের মধ্যে মামদানির সমর্থন ছিল সর্বাধিক। ব্রুকিংস ইনস্টিটিউটের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, তরুণ ভোটাররা এমন রাজনীতিবিদ চান যিনি তাদের ভাষায় কথা বলেন। ডিজিটাল মাধ্যমে সংযোগ রাখেন এবং প্রতিশ্রুতিতেও স্বচ্ছ। মামদানি সেই প্রতিচ্ছবি হয়েছেন।
দ্য টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিজেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পরিচয় দিয়ে মামদানি প্রচারণার সময় বলেছেন, তাঁর প্রচারণা সম্পূর্ণ জনগণের দানে চলে, করপোরেট অনুদানে নয়। এই অবস্থান নিউ ইয়র্কের প্রগতিশীল ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের সততানির্ভর রাজনীতির প্রতীক হয়ে ওঠে।
এ ছাড়া, নিউ ইয়র্কের ভোটাররা নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের। মামদানি প্রতিটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি আলাপ করেছেন। লাতিনো কমিউনিটি থেকে ইহুদি সংগঠন, বাদ যাননি ভারতীয় কিংবা বাংলাদেশিরাও। বাংলা ভাষায় তাঁকে স্লোগান দিতেও দেখা গেছে।
এই বিষয়গুলোই ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতাসীন দল রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়ী হতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জোহরান মামদানির ‘ট্রাম্প কার্ড’ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তিনি এটিও প্রমাণ করেছেন, প্রতিনিধিত্বের রাজনীতি যখন আন্তরিক হয় তখন সেটি সীমান্ত মানে না। নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে থেকে ঢাকার সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজফিডেও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।
A Publication of MUNA National Communication, Media & Cultural Department. 1033 Glenmore Ave, Brooklyn, NY 11208, United States.